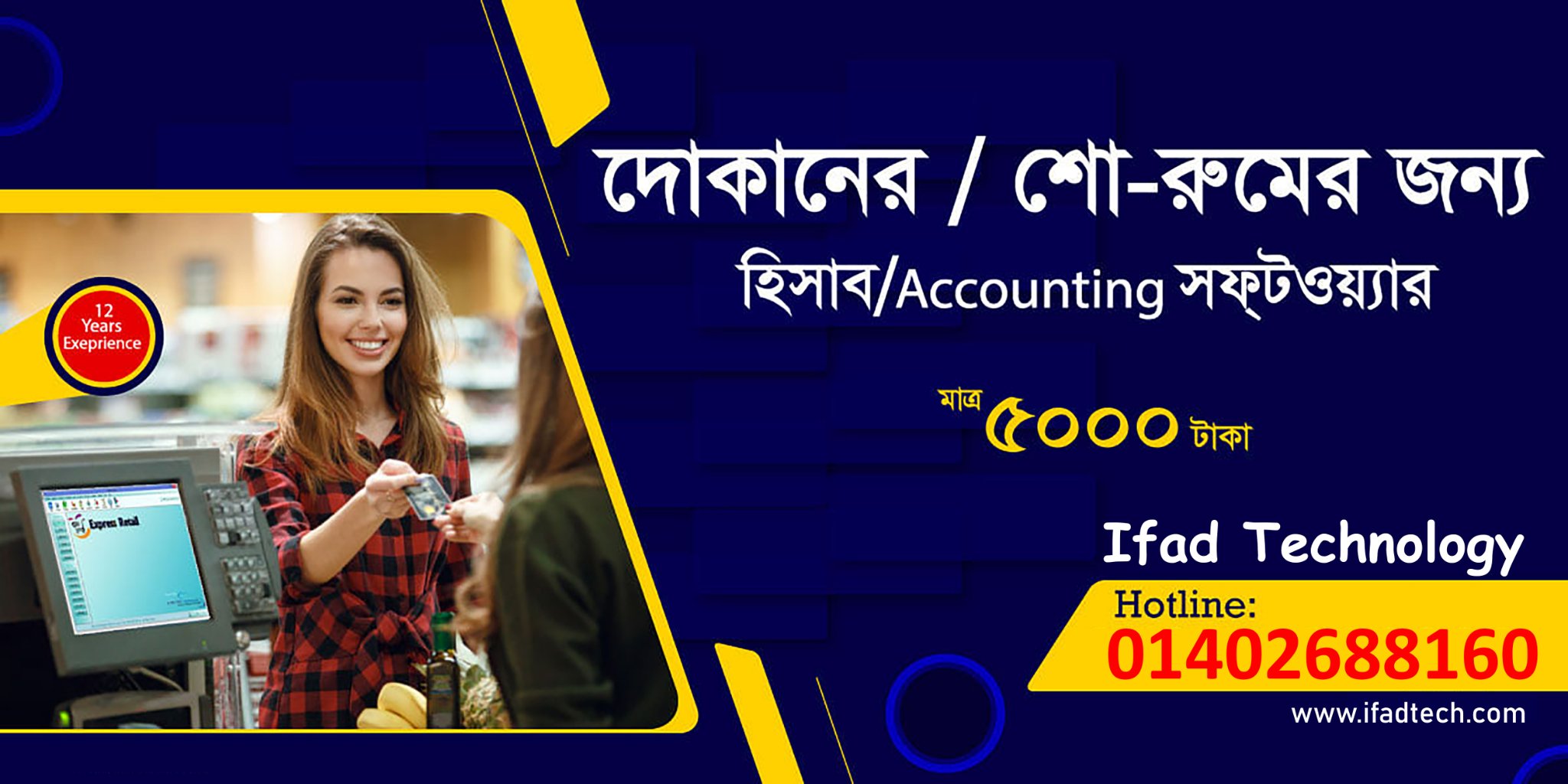গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য: শরীয়তপুরের উপেক্ষিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী

ছোট্ট মৎস্যকুমারীর কথা মনে আছে? ওই যে একদিন সে দেখেছে রাজকুমারকে এবং তারপর সে মানুষের মতো দুটি পা চেয়েছিল?
হ্যাঁ। আমি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের বিখ্যাত রূপকথা ‘লিটল মারমেইড’–এর কথা বলছি। ওখানে মৎস্যকুমারীর লেজ খসে গিয়ে পা হয়েছিল! কিন্তু প্রকৃতিতে, বিশেষ করে প্রাণিজগতে কিন্তু এমনটা সাধারণত হয় না। হাতির বাচ্চা কিন্তু একটা ছোট হাতিই। মানে এর হাত, পা, শুঁড়—সবই থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আনুপাতিক হারে বাড়ে। মানুষের বেলায়ও তা–ই। কোনো ব্যতিক্রম কি মনে পড়ে?
হ্যাঁ। ব্যাঙ। ছোটবেলার ব্যাঙ হলো ব্যাঙাচি—লেজ থাকে, কানকো থাকে। কিন্তু ব্যাঙ হতে হতে লেজ খসে পড়ে, জন্মায় পা। প্রকৃতির এই বিরল ঘটনা মানুষ প্রথম থেকে লক্ষ করেছে। তবে কেউ কিন্তু ভাবেনি, আচ্ছা, কী করলে ব্যাঙাচি আর ব্যাঙ হতে পারবে না? বড় ব্যাঙাচিই রয়ে যাবে?
শরীয়তপুর জেলায় জন্ম এ রকম একজন বাঙালি প্রকৃতিবিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম এমনটা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন, পরিবেশের যেহেতু একটা প্রভাব আছে জীবনের ওপর, তাহলে নিশ্চয়ই এখানেও এমন কিছু সম্ভব। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরের মূল কারণ আয়োডিনজনিত থাইরক্সিন হরমোন। কিন্তু গোপালবাবু দেখলেন যদি ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করা যায়, তাহলে আর সেটি ব্যাঙ হয় না, বড় ব্যাঙাচিই থেকে যায়! গোপালবাবু যখন এই গবেষণা করছিলেন, তখন কলকাতায় এসেছিলেন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জুলিয়ান হাক্সলি। তিনি খুব অবাক হলেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় বিষয়টি ছাপিয়ে রাখতে। তা সেটা আর করা হলো না!
তো যে লোকটা এ রকম দিনের পর দিন পানির মধ্যে একটি ব্যাঙাচি রেখে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তাঁর সে গুণ কিন্তু ছোটবেলা থেকেই দেখা যাওয়ার কথা।
১ আগস্ট ১৮৯৫ সালে আমাদের এখনকার শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার একটি গ্রামে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্ম। বাবা অম্বিকাচরণ কুলীন ব্রাহ্মণ। পেশা যজমানি। মানে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে পূজা-পার্বণ করে দেন। মা শশীমুখী। গোপাল বড় ছেলে এবং তারপর তাঁদের আরও চারটি ছেলে–মেয়ে হয়। কিন্তু গোপালের পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান। বেচারি শশীবালা নিদারুণ অর্থকষ্টে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করেন। বড় ছেলে হিসেবে সে কাজে গোপালকে জড়িয়ে পড়তে হয়। এর মধ্যে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে গোপালচন্দ্র ভর্তি হন লোনসিং বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯১৩ সালে মেট্রিক পাস করেন। তারপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আইএ ভর্তি হন। কিন্তু কয়েক দিন পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ফলাফল গোপালচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
গ্রামে ফিরে গিয়ে তিনি ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ওই লোনসিং বিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকে জলে–জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর একটা নেশা ছিল তাঁর। তবে গাছগাছালি থেকে তাঁকে বেশি টানত পোকামাকড়। পিঁপড়া, মাকড়সা, গুবরে পোকা এগুলো ধরে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। যোগেন নামে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন ওই স্কুলে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন, ‘মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের কতকগুলি বিচি বের করে টেবিলের ওপরে রাখার পরেই একটি বিচি প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি থেকে থেকে লাফাতে শুরু করে দিল।…অবশেষ মাস্টার মশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে ফেলতেই দেখা গেল তার ভেতরে একটা পোকা (লার্ভা)।’
এ ঘটনা তাঁকে আরও বেশি পোকামাকড়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি তিনি প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনা, বিশেষ করে প্রচলিত ভৌতিক বিষয়ও তলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় রাতের বেলায় গ্রামের জল-জঙ্গলের ধারে হঠাৎ হঠাৎ আলো দেখা যেত—আলেয়া। লোকে বলত, ভূতের আগুন। তো ভূত দেখার লোভে গোপালচন্দ্র একদিন এক বন্ধুকে নিয়ে রাতের বেলায় রওনা দিলেন আলেয়া দেখার জন্য।
লক্ষ্য ‘পাঁচীর মার ভিটা’। অমাবস্যার রাত। গা–ছমছমে ব্যাপার। একদিন ভূতের আলো দেখার জন্য দুই বন্ধু মিলে রাতের আঁধারে গিয়েছিলেন ‘পাঁচীর মার ভিটা’ নামের একটি স্থানে। সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছে। হাতে হারিকেন, ছাতা ও ম্যাচ। ঝোপঝাড় পেরিয়ে পৌঁছালেন ভিটার কাছে। হারিকেনটা একটু কমিয়ে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখলেন অস্পষ্ট আলো। সাহস করে আরেকটু কাছে যেতেই দপ করে জ্বলে উঠল। কিছুটা লাফালাফি করে এবার যেন স্থির হলো। আরও একটু সাহস করে সামনে এগোতেই দেখলেন আগুনের কুণ্ডলী কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আগুনের কোনো শিখা নেই। কয়লা পুড়লে যেমন আগুন হয়, তেমন জ্বলজ্বল করছে। আলোটার তীব্রতা নেই, কিছুটা নীলাভ। এই আলোয় চারপাশের কিছু অংশের ঘাস, লতাপাতা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আরও কাছে যেতেই দেখলেন, পুরোনো একটা গাছের গুঁড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। গুঁড়ির কাছেই একটা কচুগাছের পাতা এদিক–ওদিক দোল খাচ্ছে। এই পাতার জন্যই দেখা যাচ্ছিল, আলোটা একবার নিভছে আবার জ্বলছে। তিনি গাছের গোড়া থেকে কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। পরে বুঝলেন, আসলে জমে থাকা জৈব পদার্থ পচে মিথেন গ্যাসে পরিণত হয়, আর সেটিই বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে। এই হলো ভূতের আলো।
গ্রামে বেশি দিন থাকা সম্ভব হলো না আর্থিক সংকটের কারণে। পাড়ি জমালেন কলকাতায়। চাকরি নিলেন কাশীপুরে অবস্থিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের কথা মনে করতেন। পোকামাকড়ের ঘরবসতি নিয়ে ভাবতেন। কলকাতার বাসার আশপাশে মাকড়সা, পিঁপড়া এগুলো দেখাও অব্যাহত রাখলেন। এর মধ্যে একদিন লিখে ফেললেন আলেয়া নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত। পাঠিয়ে দিলেন প্রবাসী পত্রিকায়। প্রবাসী পত্রিকায় গোপালচন্দ্রের নিবন্ধ চোখে পড়ল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। জগদীশচন্দ্র বসু তখন মাত্র বসু মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। খুঁজে ফিরছেন তাঁদের, যাঁদের পর্যবেক্ষণক্ষমতা ভালো। জগদীশচন্দ্র বসুর আগ্রহে ১৯২১ সালে গোপালচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দিরে যোগ দেন। তখন থেকে তাঁর গবেষণার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।
সেই বছর বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আসেন জার্মান প্রকৃতিবিজ্ঞানী হ্যানস মলিশ। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয় তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য। ছয় মাসের এই কাজের ফলে প্রকৃতি ও প্রাণী পর্যবেক্ষণের কাঠামোগত ব্যাপারটিও তিনি রপ্ত করে ফেলেন। দুজন মিলে কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ, গতিপ্রকৃতি, খাদ্য সংগ্রহের কৌশল, বংশবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। ফলে কীটপতঙ্গ ও লতাপাতা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পায়। সহকারী হিসেবে তাঁর একটি কাজ ছিল ছবি আঁকা। সেটিতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তখন তাঁকে ছবি তোলা শিখতে বলেন এবং পরে কিছুদিন তিনি আচার্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ওপরও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। সহায়তা করতে করতে একদিন তিনি নিজেও একা একা গবেষণা করতে শুরু করেন।
বসু বিজ্ঞানমন্দিরে থাকতে গোপালচন্দ্র নালসো পিঁপড়া (লাল পিঁপড়া নামে পরিচিত) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি পিঁপড়ার কলোনিকে স্বচ্ছ সেলোফেন দিয়ে ঢেকে রাখলেন আর দিনের পর দিন সেগুলোর আচরণ লক্ষ করলেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ তিনি প্রকাশ করেন ১৯৪০ সালে। সেখানে তিনি দেখান, পিঁপড়াগুলোর খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে এগুলোর যথাক্রমে রাজা, রানি, কর্মী ও সৈনিক পিঁপড়া হওয়ার সম্পর্ক আছে। সে সময় ধারণা ছিল, জিনই মনে হয় একমাত্র কারণ। কিন্তু গোপালচন্দ্রের গবেষণায় বোঝা গেল, না, জিনগত কারণ ছাড়াও খাদ্যাভ্যাসও পিঁপড়ার শ্রেণিভেদের অন্যতম কারণ। গোপালচন্দ্রের এই আবিষ্কারের চার দশক পরে ১৯৮০ সালে দুজন পিঁপড়া বিশেষজ্ঞ একই বিষয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র তাঁর যথাযথ স্বীকৃতি পাননি।
কীটপতঙ্গের জগতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারটা কম, সহজাত প্রবৃত্তি বেশি। কিন্তু গোপালচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, একধরনের কুমড়াপোকা কানকোটারির ব্যবহার। অন্যান্য পোকার মতো এগুলোও নিজেদের ডিম রক্ষা করার চেষ্টা করে, তবে সে জন্য সেগুলো কেবল সহজাত প্রবৃত্তিতে চালিত হয় না। কানকোটারি নিজেদের পায়ের মধ্যে কাদা লাগিয়ে নেয়। তারপর কাদাগুলো শুকিয়ে গেলে সেটি মুক্ত হয়ে যায়। এ যেন পায়ে শক্ত বুট পরা। তারপর কোনো শত্রু ডিমের কাছে এলে সেটিকে এই বুট পরা পা দিয়ে লাথি দেয় কানকোটারি!
বসু বিজ্ঞানমন্দিরে থাকাকালে গোপালচন্দ্র গবেষণা করেছেন বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় নিয়ে। তার মধ্যে ব্যাঙাচি, শুঁয়াপোকা, মাছখোকো মাকড়সা, বোলতা ইত্যাদি পোকামাকড়ের জীবন ও বৈচিত্র্য। স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার আচার–আচরণ ও গতিবিধি, শক্তি ও অবস্থান, ডিম দেওয়া ও এর যত্ন, স্ত্রী মাকড়সার প্রতি পুরুষ মাকড়সার আচরণ, স্ত্রী মাকড়সা কর্তৃক পুরুষ মাকড়সার গলাধঃকরণ। শুঁয়াপোকা, প্রজাপতি, পিঁপড়া ইত্যাদির জীবনরহস্য। এ সময় তিনি কীটপতঙ্গ ও লতাপাতা বিষয়ে ১৬টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এগুলোর বেশির ভাগ প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাঁর লেখা কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মুখপত্র, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকায়। বাংলার ‘পিপীলিকা অনুকারী মাকড়সা’ প্রবন্ধে একটি নতুন প্রজাতির লাল পিঁপড়া অনুকারী মাকড়সার নিজের মেয়ের নামে নামকরণ করেন Propostira ranii। (রানী গোপালচন্দ্রের একমাত্র কন্যার নাম)। পিঁপড়া, মাকড়সা, ব্যাঙাচি ও ফড়িংয়ের ওপর অনেক ছবি তোলেন। তাঁর প্রায় ২২টির মতো নিবন্ধ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।
১৯৪৯ সালে গোপালচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির ছেড়ে চলে আসেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে। দায়িত্ব নেন এর মুখপত্র—বিজ্ঞান সাময়িকী জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার। ১৯৫১ সালে ভারতের কীটপতঙ্গের ওপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো সেখানে একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তাঁকে উপেক্ষা করা হলে তিনি মনঃকষ্ট পান। অথচ ১৯৪০ সালের আগেই গোপালচন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন।
করে দেখো নামে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তিন খণ্ডের একটি বিখ্যাত বই রয়েছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে তিনি শিশু–কিশোরদের উপযোগী করে প্রায় ৮০০ নিবন্ধ লেখেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৬৮ সালে পান আনন্দ পুরস্কার। ১৯৭৪ সালে লাভ করেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক, ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাঁকে দেওয়া হয় জাতীয় সংবর্ধনা। ১৯৭৫ সালে বাংলার কীটপতঙ্গ গ্রন্থের জন্য তিনি পান রবীন্দ্র পুরস্কার।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ সালের ২১ জানুয়ারি তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করে।
১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।
লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড